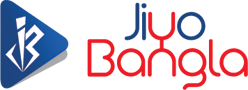তন্ত্র শাস্ত্র অনুযায়ী এই দেবীকে সরস্বতীর আর এক রূপ বলে মনে করা হয়। তিনি বিদ্যা ও সঙ্গীতের দেবী। কিন্তু দেবী সরস্বতীর স্নিগ্ধতা তাঁর মধ্যে নেই। ‘দশমহাবিদ্যাতন্ত্র’-য় তাঁকে পরমতম জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।
ঘোর দর্শনা এই দেবী দশমহাবিদ্যার নবম মহাবিদ্যা-দেবী মাতঙ্গী। মতঙ্গাসুরকে বিনাশ করার জন্য দেবীকে মাতঙ্গী বলা হয়। মাতঙ্গীর দেহবর্ণ সবুজ, তাঁর এক হাতে বীণা, অন্য হাতে তরবারি, মহাখর্পর এবং বরাভয়। তাঁর সঙ্গী হিসেবে টিয়াপাখিকে কল্পনা করা হয়। তাঁর মাথায় থাকে অর্ধচন্দ্র, আর তিনি রক্তবস্ত্র পরিহিতা। দেবীর চার হাত, যা চারটি বেদের প্রতীক মনে করা হয়। এক হাতে বীণা ছাড়াও বাকি তিন হাতে তাঁর নরকরোটি, বরাভয় এবং খড়্গ থাকে।
আর এক মত অনুযায়ী, দেবী হলেন মাতঙ্গ নামক এক মুনির কন্যা। মাতঙ্গ মুনি পুরাকালে বন্য প্রাণীদের বশ করার হেতু ত্রিপুরাদেবীর সাধনা করছিলেন। দেবী যখন দেখা দেন, তাঁর নেত্র থেকে এক জ্যোতি নির্গত হয়। এই জ্যোতি এক শ্যামলা, ষোড়শী এবং অপরূপ দেবীমূর্তি ধারণ করে। এই দেবীর নাম রাজমাতঙ্গিনী।
মাতঙ্গীকে ‘উচ্ছিষ্ট-চণ্ডালিনী’ বলে উল্লেখ করে অসংখ্য তন্ত্রগ্রন্থ। এই মহাভয়ঙ্করী দেবী তুষ্ট হন এঁটো-কাঁটা আর নোংরায়। তাঁর পূজা ও ভোগ প্রদানের যে বিধান শাস্ত্রে রয়েছে, তা এই প্রকার— অপরিষ্কার হাতে এঁটো খাবার তাঁকে নিবেদন করতে হবে।
কিন্তু কেন এলো বিধান?
‘প্রাণতোষিণী তন্ত্র’ অনুসারে, একদা পার্বতী তাঁর বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য শিবের কাছে আবদার করেন। শিব কোনভাবেই রাজী ছিলেন না। কিন্তু দেবীর জেদের কাছে নিমরাজী হয়ে শর্ত দেন, দেবী কয়েক দিনের মধ্যে ফিরে না এলে তিনি স্বয়ং তাঁকে আনতে যাবেন। উপায় না দেখে এই শর্তেই রাজী হন পার্বতী। বাপের বাড়ি গিয়ে স্বামীগৃহে ফিরতে তিনি দেরী করেন।
শিব এক অলঙ্কার বিক্রেতার ছদ্মবেশে হিমালয়-গৃহে পৌঁছন এবং পার্বতীকে একটি শাঁখা বিক্রয় করেন। সেই সঙ্গে তিনি পার্বতীর সঙ্গে মিলন কামনা করেন। পার্বতী ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে শাপ দিতে উদ্যত হন। কিন্তু অচিরেই তিনি শিবকে চিনতে পারেন। এবং জানান, যথা সময়ে তাঁদের মিলন সম্ভব হবে।
এই মিলনের অভিপ্রায়ে পার্বতী চণ্ডালিনীর বেশ ধরেন এবং মিলিত হন। শিব তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। দেবী চণ্ডালিনী রূপে পূজিতা হওয়ার বর চান। শিব তাঁকে তাই দান করেন। শিব সেই প্রার্থনা পূরণ করেন। তিনি দেবীকে বলেন, যে কোনও শক্তি পুজোর শেষে দেবীর এই রূপের পুজো করতে হবে। অন্যথায় সেই শক্তিপুজো বিফলে যাবে।
বারাণসীর লোককথা অনুযায়ী, মাতঙ্গী দেবীর উপাসনা যুক্ত ছিল চণ্ডাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে। সে কারণে, তাঁর চণ্ডালিনী রূপটি গড়ে ওঠে। তাঁকে শ্মাশানবাসী, ভস্ম মাখা শিবের যোগ্য শক্তি বলে মনে করা হয়। এই কারণেই তিনি উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারিণী, অপরিচ্ছন্না। মাতঙ্গীর উপাসনা মানুষকে ক্লিন্নতা থেকে মুক্ত করে।
এই দেবীর পূজা পদ্ধতি অতি গোপন এবং ভয়াবহ। ‘গূহ্যাতিগূহ্য তন্ত্রম্’ অনুসারে মাতঙ্গী উপাসনা ডামরীশক্তিকে জাগ্রত করে, সাধকের পক্ষে সেই ভায়নক শক্তিকে সামলানো সব সময়ে সম্ভব হয় না। ডামরীকে মাতঙ্গীর উপদেবী বলে অনেকেই মনে করেন। ডামরীও অপরিচ্ছন্না।
বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে মাতঙ্গী জয়ন্তী পালিত হয়। এই দিন পূজিত হন দেবী মাতঙ্গী। দেবী দুর্গার আর এক রূপ হিসেবেই তিনি পূজিতা।
 In English
In English