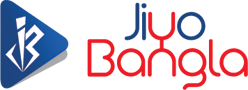রাজবাড়ি, জমিদার বাড়ি, ধনীর ঠাকুরদালানের মা দুর্গা এখন সর্বজনীন দেবী। সর্বজনের মিলিত প্রয়াসে তাঁর পুজো হয়। যার মাধ্যম হল চাঁদা, বারোয়ারি পুজোর মূল ভিত্তি। সকলে চাঁদা দিয়ে দেবীর পুজো করেন, তাই সর্বান্তকরণে সার্থক হয় সর্বজনের দুর্গা আরাধনা। সকলে সামিলও হন চাঁদা দেওয়ার মধ্যমেই। একেবারে প্রথম বারোয়ারি পুজোর সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদা সংস্কৃতির জন্ম। হুগলির গুপ্তিপাড়ার কোনও এক বনেদি বাড়ির কর্তা আর্থিক সংকটে পড়েন। ১৭৯০ সাল নাগাদ বন্ধ হয়ে যেতে বসে তাঁর বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনী পুজো। এগিয়ে আসেন স্থানীয় বারোজন ব্রাহ্মণ। তাঁরাই চাঁদা তুলে পুজোর আয়োজন করেন। ১২ জন ‘ইয়ার’ বা ‘বন্ধু’ থেকেই ‘বারোয়ারি’ শব্দের উৎপত্তি। এভাবেই শুরু হয় ‘বারোয়ারি’ তথা সর্বজনীন দুর্গাপুজো। শ্রীপান্থ তাঁর স্মৃতির পুজো গ্রন্থে লিখেছেন, ‘‘সেকালের সাংবাদিকেরা এই পুজো সম্পর্কে লিখতেন বার-এয়রি। হুতোম বলতেন বারোইয়ারি।’’
যে বারোজন ব্রাহ্মণ চাঁদা তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁদের কেউ কেউ আবার চাঁদার খাতা সহ উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। পরে ফিরে বলেছিলেন, খাতা হারিয়ে গিয়েছে। হিসাবে নেই। প্রথম বারোয়ারি পুজোয় চাঁদা উঠেছিল সাত হাজার টাকা। প্রতিমা, পুজোর খরচ ছাড়াও গান, বাজনা, বাঈনাচের আসর বসেছিল চাঁদার টাকায়। অনেক জমিদারের পক্ষেই চারদিন ধরে পুজো চালানোর ক্ষমতা ছিল না। তাঁরা সঙ্গত কারণেই চাঁদার দিকে ঝোঁকে। সেই চাঁদা সংস্কৃতি আজও অক্ষত এবং ওতপ্রোতভাবে এখনও জড়িত পুজোর সঙ্গে।
কোথাও কোথাও তা জুলুম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এ জুলুম আদিকাল থেকেই রমরমিয়ে চলছে। উনিশ শতকে থানা পুলিশ অবধি গড়িয়ে গিয়েছিল চাঁদার কাণ্ড! বেহালার বারোয়ারিতলা দিয়ে লোকজন যাতায়াত করতে পারত না। কারণ চাঁদার উপদ্রব। মহিলাদেরও রেহাই ছিল না। ছেলে ছোকরার দল জুলুম করত। নিরুপায় হয়ে দেশবাসী ইংরেজ প্রশাসনের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ভারতীয়দের শিক্ষা দিতে এমনিতেই ভালবাসতেন সাহেবের দল। এবারেও ময়দানে নামলেন।
১৮৪০ সালের ঘটনা। বারোয়ারিতলায় চাঁদার জুলুম চলছে। পথিক থেকে পালিক, কেউই রেহাই পাচ্ছেন না। একদিন কলকাতা থেকে সুসজ্জিত পালকি রওনা দিল বেহালার উদ্দেশে। সুন্দর দামি পালকি, ভেলভেট জড়ানো, সঙ্গে রেশমি ঝালর। এক পলক দেখলে মনে হবে কোনও বিত্তবান বাড়ির বধূ চলেছেন তাতে। বেহারাদের কাঁধে চেপে পালকি এসে পৌঁছল বেহালায়। সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ি ফেলে বেহারারা বামদিকের পথ ধরল। বাঁ দিকেই ছিল বারোয়ারিতলা। যেই না বারোয়ারিতলায় পৌঁছল পালকি সঙ্গে সঙ্গে হাজির চাঁদা আদায়কারী ছেলে ছোকরার দল। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল হুকুম। ‘পালিক থামাও!’ টাকা না-দিলে পালকি ছাড়া হবে না। অমন সাজগোজ দেখে তারা ভেবেছিলেন কোনও ধনী পরিবারের কন্যা বা বধূ চলেছেন। ভাল টাকা আদায় হবে।
ফের হুকুম এল বেহারাদের প্রতি, বধূকে বের কর, টাকাপয়সা আছে কি-না দেখব। পালকির দোরের পর্দা সরাতেই চক্ষু চড়কগাছ। পালকির ভিতরে শাড়ি পরে বসে রয়েছে এক সাহবে! পেটন সাহেব। চব্বিশ পরগনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। চাঁদাবাজদের ঠান্ডা করতেই তাঁর মহিলা বেশ। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনকে আটক করলেন সাহেব। কড়া শাস্তিও দিলেন। এরপর থেকে চাঁদার জুলুম দমে গিয়েছিল কলকাতায়।
তবুও দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়লে পাড়ার ছেলের দল চাঁদা কাটতে বের হয়। বাঙালির মনে উৎসবের মরশুম হিল্লোল তোলে। পুজোর চাঁদা কাটতে আসা মানেই ‘পুজো আসছে আসছে’ ভাব। বিলে টাকার অঙ্ক দেখে মধ্যবিত্ত বাঙালির বুক ধড়ফড়, কষাকষি। চাঁদা কেটে ঘামে ভিজে বাড়ি ফেরা। কারও বাড়িতে একটু জল চাওয়া। চাঁদা সংস্কৃতিও যেন দুগ্গাপুজোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।
 In English
In English