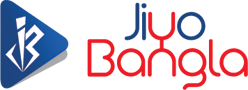বাঙালি কন্যা রূপে দুর্গার পুজো করে, আবাহন করে এবং আরাধনা শেষে বাড়ির মেয়েকে পতিগৃহের উদ্দেশে রওনা করে দেয়। তাই বাংলার দুর্গা, বাঙালির দুর্গা পূজিতা হন সপরিবারে। বঙ্গে দুর্গাপুজোর প্রচলনকারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন রাজা কংসনারায়ণ, তিনিও পুত্র-কন্যা সহ দুর্গার পুজো করেছিলেন। সেই রূপের দেবী অধিক জনপ্রিয় এবং পূজিতা হন আজও। মৃৎশিল্পী, পটুয়া, কারিগরদের ভাষায় এ হল ‘সাত-পুতুলে দুর্গা’।
দুর্গা প্রতিমা কাঠামোয় থাকেন ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মী, জ্ঞানের দেবী সরস্বতী, যুবশক্তি ও বীরত্বের দেবতা কার্তিক এবং সাফল্যের দেবতা গণেশ। মহিষাসুর অশুভ শক্তির প্রতীক। লক্ষ্মী বৈশ্য শক্তির প্রতীক। গণেশ জনগণের ঈশ্বর, তিনি সিদ্ধিদাতা। গণেশ গণশক্তি অর্থাৎ শূদ্রশক্তির প্রতীক। সরস্বতী জ্ঞানমূর্তি ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রতীক। দেবসেনাপতি কার্তিক শক্তি, বীরত্ব, শৌর্য বীর্যের প্রতীক। একচালি প্রতিমায় মা দুর্গা স্বামী-সন্তানদের নিয়ে একটি চালে অবস্থান করেন। মাঝখানে মা দুর্গা, ডানে লক্ষ্মী ও গণেশ এবং বামে সরস্বতী ও কার্তিক। চরণতলে বাহন সিংহ এবং সামনে বামদিকে অসুর। গণেশের পাশে কলা বৌ এবং মাথার ওপর শিব। কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় কার্তিক, গণেশ ও কলা বৌয়ের অবস্থানে। কালে এক চালা ভেঙে গিয়েছে, দুর্গা ও অসুর একসঙ্গে এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আলাদা প্রতিমার প্রচলন হয়। যা প্রধানত সর্বজনীন পুজোয় দেখা যায়।
দেবী তো মহিষাসুরমর্দিনী। প্রথম শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে সেই রূপেই দেবী পুজো পেয়ে এসেছেন। মহিষমর্দিনী দেবীর প্রতিমার সঙ্গে সন্তান-সন্ততিরা যুক্ত হলেন কবে থেকে?
শ্রীশ্রী চণ্ডীতে রয়েছে, মহিষাসুরের সংহার করতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবতাদের তেজ মিলিত হয়ে মহামায়ার আবির্ভাব হয়েছিল। চণ্ডীতে কোথাও লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের উল্লেখ নেই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অর্থাৎ শ্রীরাম পাঁচালি অনুযায়ী, রামচন্দ্র অকালবোধনে মহিষাসুরমর্দিনী দেবীরই পুজো করেছিলেন।
মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে, দেবী যথাক্রমে মধু-কৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন। অন্তিম সময়ে দেবী দুর্গার কাছে পরাজিত মহিষাসুর প্রার্থনা করেছিলেন, দেবী যেন মহিষদেহকে নিজের বাহকরূপে গ্রহণ করেন। দেবী তাতে সম্মতও হয়েছিলেন। উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী, দুর্গা; তিনবার তিনরূপে দেবী মহিষাসুরের নিধন করেন। মহিষাসুরের প্রার্থনা মেনে তিন রূপেই দেবী মহিষাসুরকে পদতলে ঠাঁই দেন। আজও দুর্গাপ্রতিমায় মহিষের মুণ্ডের উপস্থিতি দেখা যায়। দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরও পুজো পান।
প্রথম শতকের যেসব দুর্গা মূর্তি পাওয়া যায়, প্রতিটি মূর্তিতেই দুর্গা অসুরঘাতিনী। কুষাণ যুগের ভাস্কর্যেও কেবলই দুর্গার দেখা মেলে। মার্কেণ্ডয় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, কালিকা পুরাণেও দেবী এককভাবেই রয়েছেন, কোথাও পরিবারের চিহ্ন নেই। নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে তিনি হয়ে উঠলেন পরিবারের কর্ত্রী। ওই সময়কালের মধ্যে বিহার, দিনাজপুর থেকে উদ্ধার হওয়া ভাস্কর্য, ফলকে তিনি মাতৃরূপা, সপরিবারে আবির্ভূতা।
‘সপরিবারায়ৈ শ্রী দুর্গায়ৈ বৌষট’- এ মন্ত্র চণ্ডীতে নেই। বাঙালি স্বয়ং এই মন্ত্রের স্রষ্টা। কারণ, সে যে দেবী দুর্গার পুজো করে, সে গৃহকর্ত্রী দুর্গা। সংসারের মাথা। সপরিবারে দুর্গাকে আবাহন করে, নিবেদন করে, বিদায়বেলায় বরণ সেরে মিষ্টিমুখ করিয়ে বলে, ‘আবার এসো’। ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রতি বছর বাপের বাড়ি আসা দেবী খাঁটি বাঙালি কন্যা।
আদপে দুর্গার এই পারিবারিক রূপ বাঙালিয়ানার ফসল। পুরাণকার এবং কবিদের সৃষ্টি কবি রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে দুর্গাকে করে তুলেছেন বাঙালির ঘরের মেয়ে। তাঁদের হাতেই শিব হয়েছেন দুর্গার স্বামী। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী চালচিত্রের উপরে, একেবারে মাঝে থাকেন শিব। রায়গুণাকর, মুকুন্দ চক্রবর্তীরাও সেভাবেই দেবীকে গড়েছেন। বাঙালিয়ানা ও বাংলার বৈষ্ণব ধারার অভিঘাতে কোথাও কোথাও দুর্গাপ্রতিমা থেকে মহিষাসুরের অবলুপ্তি ঘটলেও, দেবীর পরিবার সর্বত্র বিরাজমান। জয়া, বিজয়া, পুত্র-কন্যাদের নিয়ে তিনি পূজিতা হন।
 In English
In English