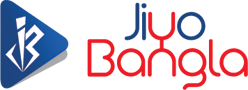বঙ্গদেশ হল মহামিলন ক্ষেত্র। বহু সাধনপথের মিলিত ধারা বাংলার আধ্যাত্মবাদকে সমৃদ্ধ করেছে। যার মূল পথ দুটি, একটি শাক্ত, অপরটি বৈষ্ণব। সভ্যতার আদিকাল থেকে শক্তির উপাসনা করে চলেছে আর্যাবর্ত। মাতৃ আরাধনাও তো শক্তির আরাধনা। অন্যদিকে, পঞ্চদশ শতকে শ্রীচৈতন্যের হাতে ধরে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মমতের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। বাংলার সর্ববৃহৎ উৎসব দুর্গাপুজোতেও শাক্ত ও বৈষ্ণবের দুই ধারা দেখা যায়। দুর্গাপুজোর বয়স হাজার বছরেরও বেশি। বনেদিবাড়ির রেওয়াজ মেনেই দেবী পূজিতা হতেন। আড়াইশো তিনশো বছর আগেই দুর্গাপুজো, দুর্গোৎসবের রূপ নেয়। সর্বজনের পুজো হয়ে উঠে। কিন্তু আজও শাক্ত ও বৈষ্ণব, দুই ধারাপথে দেবীর পুজো হয়।
শাক্তের দেবী সর্বসংহারিণী, কিন্তু বৈষ্ণবের দেবী অভয়দায়িনী। শাক্ত ও বৈষ্ণব পরিবারের দুর্গাপুজোর মূল ফারাক রয়েছে আরাধনার লক্ষ্যে। শাক্তরা দুর্গাকে পরমশক্তি রূপে পুজো করেন। কামনা থাকে ইহজাগতিক। প্রার্থনা থেকে চাহিদা পূরণের। বৈষ্ণবেরা পুজোর করেন আত্মনিবেদনের জন্য। ঈশ্বরের চরণে সোঁপে দেওয়ার জন্য। বৈষ্ণবদের কাছে দেবী দুর্গা হলেন পরমেশ্বরীর এক রূপ।
শাক্তের দেবী দুর্গার সৃৃষ্টি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের তেজ থেকে। উদ্দেশ অসুরের সংহার। ত্রিলোকের উদ্ধারে। “শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে। সর্বস্যার্তি হরে দেবী নারায়ণী নমোহস্তুতে” - শরণাগত দীনকে রক্ষা করতে দেবী নারায়ণীর আবির্ভাব। এই নারায়ণীই তো দুর্গা। মহিষমর্দিনীর আবির্ভাবের সময় সবার প্রথমে বিষ্ণুর মুখমণ্ডল থেকে নির্গত হয় জ্যোতি। “সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্রম্বক্যে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে”- সর্বমঙ্গলদায়িনী, শিবা ত্রম্বকা গৌরী নারায়ণীকে প্রণাম। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী, জগতে প্রথম দুর্গার আরাধনা করেন কৃষ্ণ- “প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা। বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদ্যৌ গোলকে রাসমণ্ডলে।”
শ্রীবিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে, দেবকীর অষ্টম গর্ভে। তাঁর সহায়ক হন দুর্গাও। বিষ্ণুর বিশেষ শক্তি জগৎ পরিচালনা করেন, বিশ্বভুবন ভুলিয়ে রাখেন মায়ায়। তাই তো তাঁর অপর নাম মহামায়া। বিষ্ণুশক্তি মহামায়াই যোগমায়া নামে অবতীর্ণ হন নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মাষ্টমীতে। বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রেখে সেই কন্যাকে নিয়ে কারাগারে ফেরেন। কংস শিশুটিকে হত্যা করতে গেলেন, শিশুকন্যা কংসের হাত ছাড়িয়ে শূন্যে উঠে গেল। প্রকট হল অষ্টভুজা দুর্গা রূপে। কংস বধের দৈববাণী দিয়ে দেবী চললেন বিন্ধ্যাচলে। বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী বলেই তিনি বিন্ধ্যবাসিনী। তিনিই শুম্ভ-নিশুম্ভে সংহারিণী। শাক্তের দেবী আদতে বিষ্ণুর শক্তি রূপ! মহাভারতে, বিষ্ণুর সহস্রনাম কীর্তনে তাঁকে একবার দুর্গ বলা হয়েছে। দুর্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ দুর্গা। তিনিই সাক্ষাৎ বৈষ্ণবী শক্তি! দেবীই বিষ্ণুর শক্তি।
এবার আসি বঙ্গে, বঙ্গের পটুয়ারা দেবী মূর্তি গড়েন। সেই রূপেই দেবী পূজিতা। শাক্তবাড়ির দুর্গা যোদ্ধাবেশী, বিনাশিনী। তাঁর বাহন সিংহ হিংস্র। বৈষ্ণববাড়ির দুর্গা শান্ত, সৌম্য। তিনিও অসুরদলিনী কিন্তু ক্ষিপ্রতাহীন। তাঁর বাহন ঘোটকমুখী সিংহ। শাক্তবাড়ির দুর্গাপুজোয় সপ্তমী, অষ্টমীতে কালীপুজো করা হয়। বৈষ্ণববাড়িতে সে বালাই নেই। শাক্তবাড়ির দুর্গা বলিপ্রিয়া। ছাগ বলি দেওয়া হয় তাঁর সামনে। রক্ত, মাংস নিবেদন করা হয়। বৈষ্ণববাড়িতেও বলি হয় তবে তা মাছ, মাংসের অনুকল্প হিসাবে। বলি দেওয়া হয় আখ, চাল কুমড়ো, লাউ ইত্যাদি। শাক্তবাড়িতে দেবীকে আমিষ ভোগ নিবেদন করা হয়। অন্ন ভোগ নৈবেদ্যে দেওয়া হয়। বৈষ্ণববাড়িতে ভোগ সম্পূর্ণ নিরামিষ। ময়দার জিনিস, মিষ্টান্ন ইত্যাদিই বেশি থাকে নৈবেদ্যে। পুজোর আচার, দেবীর মূর্তিতে এই ধরনের ফারাক দেখা যায়। পুজো পদ্ধতিতেও রয়েছে অনেক পার্থক্য।
তবে কোথাও গিয়ে যেন শাক্ত আর বৈষ্ণব মিশে গিয়েছে বঙ্গে। নবদীপের শাক্তরাস যেন সে কথাই স্মরণ করায়। আচমনের মন্ত্রে রয়েছে, “ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্যেষু মাধব॥” অর্থাৎ বাক্যে মাধব, হৃদয়ে মাধব, সর্বকার্যে মাধব। মাধব হলেন শ্রীহরি। শাক্তের পুজোও শুরু হয় শ্রীহরি কৃষ্ণকে স্মরণ করে। চৈতন্যচরিতামৃতে রয়েছে “অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম। সেই ত বৈষ্ণব, করিহ তাহার সম্মান॥” অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণনাম করেন তিনিই তো বৈষ্ণব। যুগে যুগে শাক্ত আর বৈষ্ণবের আরাধনাপথ মিলিত হয়ে ঋদ্ধ করেছে বাংলার ঈশ্বরচেতনাকে।
 In English
In English