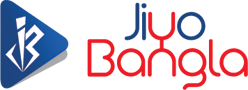‘বিরহড়’ কথাটির মানে—‘জঙ্গলের মানুষ’। এরা মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদিম উপজাতি। কিন্তু এদের সেই আদিম জীবনের প্রকৃত ইতিহাস নেই, আছে শুধু কিংবদন্তি। কী সেই কিংবদন্তি? বলছিঃ
বহুকাল আগে কাইমুর পাহাড়ে থাকত সাতভাই। একদিন সেখান থেকে চারজন গেল পুব দিকে, আর বাকি তিনজন গেল রামগড় রাজ্যে। তারপর কী কারণে যেন সেখানকার রাজা একদিন তাদের বিরুদ্ধে তেড়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন।
তখন তিনভাই, তিন বীর চলল রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। যেতে যেতে হঠাৎ একজনের মুকুট গেল গাছের ডালে আটকে। এটা নিশ্চয় কোন অশুভ সংকেত!–এই ভাবনা মনে আসতেই তাদের ভয় হল। যার মুকুট সে আর এগোল না, জঙ্গলেই থেকে গেল। তখন অন্য দু’ভাই কী আর করে, দু’জন দু’জনের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করতে গেল। অচিরেই রাজার সঙ্গে তাদের ভীষণ যুদ্ধ হল। যুদ্ধে দুই ভাই জয়ী হল। ফেরার সময় তারা আবার সেই জঙ্গলের পথ ধরল।
পথে চলতে চলতে তারা একসময় সেখানে যাওয়া ভাইকে কাঠ কেটে গাছের ছাল তোলার কাজে ব্যস্ত দেখতে পেল। তখন মজা করে তারা তাকে ‘বিরহড়’ বলে ডাক দিল। মুন্ডারি ভাষায় এর মানে হল, ‘জঙ্গলের মানুষ’। এভাবে একে-অপরকে আবার ফিরে পেয়ে যার পর নাই খুশি হল, ছুটে পরস্পরের নিকটে এসে হাত ধরল। দুই ভাই এবার জঙ্গলের ভাইকে আনন্দের সঙ্গে জানালো তাদের যুদ্ধজয়ের খবর। বলল যে, তারাই এখন রামগড়ের রাজা। এবং জঙ্গলের ভাইকে তাদের সঙ্গে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধও জানাল।
কিন্তু জঙ্গলের ভাই জয়ের খবরে অত্যন্ত খুশি হলেও তাদের প্রস্তাবে রাজি হতে পারল না। বলল যে, সে আর ফিরবে না। রাজপাটে তার প্রয়োজন নেই, বিরহড় হয়ে সে জঙ্গলেই থাকতে চায়। এই ক’দিনে সে জঙ্গলকে ভালোবেসে ফেলেছে, মুক্তজীবনের আনন্দ খুঁজে পেয়েছে। তাই এই জঙ্গল ছেড়ে সে আর কোথাও যাবে না।
সেই থেকে বংশ পরম্পরায় বিরহড়েরা জঙ্গলে থাকে, জঙ্গলকে ভালোবেসে। এরা নিজেদের বলে সূর্যের সন্তান। আর, এরা যে ভাষায় কথা বলে, তাকে বলা হয় ‘বিরহড় ভাষা’। এই ভাষার কোন লিপি নেই। পণ্ডিতদের কেউ কেউ এর সঙ্গে মুন্ডারি ভাষার মিল দেখে ধারণা করেন মুন্ডা উপজাতি থেকেই বিরহড়দের উদ্ভব। কোথাও কোথাও মুন্ডারা এদের ‘বিরমুন্ডা’ বলে ডাকে।
বিহার, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়ার জঙ্গল আর মালভূমি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই উপজাতির মানুষের দেখা মেলে। এরা সংখ্যায় অল্প। ১৯৯১ সালের জনগণনায় জানা গেছে এদের মোট জনসংখ্যা প্রায় দশ হাজার।
বিরহড়দের দুটি শ্রেণি বা গোষ্ঠী। একটি উথলু বিরহড় আর অপরটি জাগি বিরহড়। এরা মূলগতভাবে এক হলেও জীবনযাপনের দিক থেকে পৃথক।
‘উথলু’ মানে, ‘যাযাবর’। একশো বছর আগে এদের যাযাবর জীবনের অস্তিত্ব ব্যাপকভাবে থাকলেও, এখন প্রায় নেই বললেই চলে। সেই সময় একমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া এরা এক জায়গায় বেশিদিন থাকত না। তাই এরা স্থায়ী ঘর বাঁধত না। জঙ্গলের এক জায়গায় খাবার শেষ হলে এরা দল বেঁধে আরেক জায়গায় চলে যেত। একটি দলে থাকত তিন থেকে দশটি পরিবার। সঙ্গে থাকত সাংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় সাধারণ সামগ্রী। থাকত নিত্যপূজ্য পাথর বা কাঠের দেব-দেবীরাও। তবে একমাত্র অবিবাহিত যুবকই পারত এইসব দেব-দেবীদের বয়ে নিয়ে যেতে। স্থানান্তরে যাওয়ার সময় সে থাকত দলের সবার আগে। তার পিছু পিছু অন্যান্য পুরুষেরা শিকারের জাল, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র-শস্ত্র বয়ে নিয়ে যেত। আর মহিলারা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেত খেজুর পাতার চাটাই, উদুখল প্রভৃতি। পুরুষ-মহিলা সবাই সাধ্যমতো সঙ্গে নিত বাঁশের ঝুড়িতে জমিয়ে রাখা শুকনো মহুয়া ফুল ও বিভিন্ন খাদ্যশস্য। ছেলেমেয়েরা বয়ে নিয়ে যেত রান্নার উপযোগী মাটির বাসন আর পানীয় জল।
প্রয়োজনীয় শিকার আর ফলমূল মিলবে এমন একটি জায়গা বেছে এরা অস্থায়ী আস্তানা বানাত। আস্তানা বলতে গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি করে চোঙের মতো দেখতে কুঁড়ে গড়ে নিত। এদের বলা হত ‘কুম্বা’। তাতে একটি মাত্র ছোট দরজা থাকত। কুম্বায় এরা শস্য, খাবার, বাসনপত্র, শিকারের অস্ত্র, জাল প্রভৃতি রাখত আর রাত্রে মাটিতে চাটাই পেতে ঘুমোত। রান্না করতো কুম্বার বাইরে, খোলা আকাশের নীচে। কয়েকটি কুম্বা মিলিয়ে গড়ে ওঠা এই বসতিকে এরা ‘টান্ডা’ বলত।
উথলু বিরহড়েরা চাষবাসের ধার ধারত না। জীবন পুরোপুরি ছিল অরণ্যনির্ভর। জঙ্গল থেকে খাদ্য হিসেবে ফল, চুপড়ি আলু, নানান ধরনের মূল, শাকপাতা তুলে আনত। মাংসের জন্য তির-ধনুক দিয়ে হরিণ, বুনো শুয়োর শিকার করত। জাল পেতে বাঁদর, খরগোস প্রভৃতি ধরত। বুনো লতা, গাছের ছাল—এসব দিয়ে দড়ি বানাত। এই দড়ি বিক্রি করে বা এর বিনিময়ে এরা খাদ্যশস্য সংগ্রহ করত। তারপর খাদ্যের জোগানে টান পড়লেই এরা আবার নতুন ঠিকানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত।
যেহেতু উথলু বিরহড়েরা থিতু ছিল না, জঙ্গলের বাইরের সমাজের সঙ্গে তেমন যোগাযোগও ছিল না, তাই সরকারি সুযোগ-সুবিধার খবরও এরা রাখত না। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর বালাই তো ছিল না; এমনকি দেশের নামও হয়তো এরা জানত না। দেশের কথা বললে আরণ্যক ভানুমতীর মতোই হয়তো এরাও বলে উঠত, ‘ভারতবর্ষ কোনদিকে?’
উথলুরা যাযাবর হলেও জাগি বিরহড়েরা কিন্তু আজীবন স্থায়ীভাবে বাস করতেই পছন্দ করে। পাহাড়ের গায়ে, উপত্যকায় কিংবা জঙ্গলঘেঁষা টাঁড় অঞ্চলে এরা বসতি বা টান্ডা গড়ে তোলে। উথলুদের মতো ‘কুম্বা’ নয়, মাটির দেওয়াল কিংবা বাঁশ আর কাঠের বেড়ার গায়ে কাদা লেপে দোচালা ঘর বানায় এরা। ঘরের ছাউনি হিসেবে ব্যবহার করে কাশ, তাল-খেজুরের পাতা ও ঘাস। এখন অবশ্য সরকারি আবাস যোজনার বদান্যতায় এদের অনেকেরই এক কামরার পাকা বাড়ি রয়েছে।
যাই হোক, এখন প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের তথা পুরুলিয়ার বিরহড়েরা এলো কোথা থেকে?
আসলে, আজ থেকে দেড়শ বছরেরও আগে জাগি বিরহড়দের এক বা একাধিক দল রাঁচি, হাজারিবাগ ও ধানবাদ থেকে বনজ-খাবার ও শিকার-সমৃদ্ধ অঞ্চলের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে অযোধ্যা পাহাড়ে এসে হাজির হয়। প্রথমে এরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসতি গড়ে শিলিংদা, সাপারমবেড়া, ভূদা প্রভৃতি অঞ্চলে। পরে আজকের পুরুলিয়া জেলা গঠনের পর সরকারি উদ্যোগে বাঘমুন্ডির মাদলা-ভূপতিপল্লি, বাড়রিয়া, নিচিতপুর; বলরামপুরের বেড়সা; ঝালদা ১নং ব্লকের খামার টোলা ঢাকাই গ্রাম এবং বান্দোয়ানের ইঁচাহাতু গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করে। ১৯৯১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বিরহড়দের মোট জনসংখ্যা ছিল ৮৫৫ জন। এখন অবশ্য মোট জনসংখ্যা তিন হাজারের কাছাকাছি। এদের সকলেরই পদবি–‘শিকারি’।
সত্যি বলতে কী, আজ থেকে একশো বছর আগেও বিরহড়দের কোন পদবি ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে যখন সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে তারা যুক্ত হল, স্থানীয় বর্ণ-হিন্দুদের প্রতিবেশী হল; তখন অপরের অনুকরণে নিজেদেরও পদবির প্রয়োজনীয়তা তাদের মধ্যে তৈরি হল। যেহেতু তাদের আদি কোন পদবি ছিল না, শিকার ছাড়া সেই মুহূর্তে তাদের অন্য কোন জীবিকাও ছিল না; তাই এই জীবিকা বা জীবনধারণের প্রধান উপায়কেই পদবি হিসেবে ব্যক্ত করতে শুরু করল। এভাবেই ধীরে ধীরে তাদের পদবি ‘শিকারি’ হয়ে উঠল।
জাগি বিরহড়েরা স্থায়ী গ্রামজীবন পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু এদের জীবন থেকে অরণ্যনির্ভরতা কমেনি। এরা প্রায় সকলেই ভুমিহীন। তবে বর্তমানে চাষের কাজ জানে। পুরুলিয়ার অধিকাংশ জমিতেই বর্ষা ছাড়া চাষ হয় না। ফলে, এই সময় জমিতে জন খাটে, বাকি সময় অরণ্যের বদান্যতায় কাঠ-মধু-কন্দ প্রভৃতি সংগ্রহের মধ্য দিয়ে জীবন কাটায়।
বর্ষায় অন্যের জমিতে দিন মজুরি ছাড়াও বুনো লতা দিয়ে এরা এক ধরণের দারুণ টেঁকসই দড়ি বানায়, দড়িজাত সামগ্রী বানায়; স্থানীয় হাটে সেই সব বেচে সামান্য উপার্জন বাড়ায়। এই দড়ি এবং দড়িজাত সামগ্রী এদের অসামান্য কুটিরশিল্প। কিন্তু স্থানীয় বাজার ছাড়িয়ে এই শিল্প এখনও তেমন মূল্য পায়নি প্রচারের অভাবে।
যাই হোক, বিরহড়দের বিত্তহীন জীবন খুব সাদামাটা। সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে যেহেতু এখন তারা পুরোপুরি সংপৃক্ত; ফলে তাদের ব্যবহারিক জীবনে তার প্রভাবও পড়েছে। এই যেমন, একমাত্র খুব বয়স্করা ছাড়া তাদের চিরাচরিত খাটো ধুতি আর কেউ পরে না, গায়ে গামছা দেয় না। মেয়েরা হালের শাড়ি, চুড়ি পরে; ছেলেমেয়েরা ফ্রক-হাফপ্যান্ট পরে; বড়রা লুঙ্গি, বারমুডা, প্যান্টশার্ট পরে।
স্বামী-স্ত্রী আর অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছোট্ট সংসার। বাবা পরিবারের কর্তা। তার কথা সবাই মেনে চলে। তবে, সামাজিক নিয়মে ছেলের সংসার আলাদা হয়ে যায়। সাধারণত ছেলেদের কুড়ি থেকে পঁচিশ আর মেয়েদের পনের থেকে সতের বছরের মধ্যে বিয়ে দেওয়ার রীতি। বিরহড়-সমাজ এক বিবাহের কথাই বলে। তবে বিধবা হলে, স্ত্রী মারা গেলে, বন্ধ্যাত্ব ঘটলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার বিবাহ চলে। এইসব সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে বিধান দেন বিরহড়দের পুরোহিত—‘নায়া’।
দাম্পত্য ভাবনা, বিরহড়দের দেব-দেবী কল্পনাতেও আছে। সিং বোঙ্গা ও তাঁর স্ত্রী ছান্দু বোঙ্গা এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালন কর্তা। সিং বোঙ্গা সর্বশক্তিমান। বিরহড়দের প্রধান দেবতা। বিরহড়েরা মৃতদেহ পোড়ায় না, সমাধি দেয়। এরা পূর্বপুরুষের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।
বিরহড়দের প্রধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বসন্ত ঋতুর সূচনায়। এটি হল শালগাছের পুজো, ‘সরহুল’। এটি আসলে বিরহড়দের ‘বসন্ত উৎসব’। এছাড়া অনেক বছর ধরে প্রায় পাশাপাশি বাস করার জন্য অনেক হিন্দু ও আদিবাসী উৎসব, যেমন-‘মকর সংক্রান্তি’, ‘করম’, ‘দিশম সেন্দ্রা’ প্রভৃতি উৎসব বিরহড় সমাজ গ্রহণ করেছে। তবে এগুলো তারা নিজেদের মতো করেই পালন করে।
বিরহড়েরা তাদের বিশ্বাস থেকে, জীবনযাপনের গণ্ডি ছেড়ে সহজে বেরিয়ে আসতে চায় না। তাই এখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যে শিক্ষার সচেতনতা তেমন ভাবে গড়ে ওঠেনি। ভূতপ্রেত ও ডাইনিতে এখনও তারা প্রবলভাবে বিশ্বাস করে; তাদের কবল থেকে উদ্ধার পেতে এখনও তারা মাতি বা ওঝার কাছে যায়। শরীর খারাপ হলে প্রথমেই ডাক্তার নয়, জঙ্গলের শিকড়-বাকড়-বনের ওষুধেই ভরসা রাখে।
তারই মাঝে আশার কথা, টান্ডার আশপাশের সরকারি স্কুলে অনেক বিরহড় ছেলেমেয়েই এখন পড়তে আসে। তবে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে আর জীবিকার জন্য দিনভর সংগ্রাম ছেলেদের লেখাপড়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভুপতিপল্লির মঞ্জু শিকারি প্রথম বিরহড় মহিলা, যিনি মাধ্যমিক পাশ করেছেন। কিন্তু অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তাঁর আর পড়া হয়নি। বর্তমানে তিনি পেশায় একজন সাধারণ মজুর। আবার কয়েক বছর আগে সমস্ত বাধা পেরিয়ে প্রথম বিরহড় স্নাতক হওয়ার পথে অনেকটা এগিয়েও নানান সমস্যায় পড়াশুনো সম্পূর্ণ করতে পারেননি সীতারাম শিকারি। আসলে, তেমনভাবে সুযোগ পেলে বিরহড়দের মধ্য থেকে অনেকেই উদাহরণ হয়ে উঠতে পারেন, এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সমাজকে; মজবুত করতে পারেন নিজেদের সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই।।...
 In English
In English